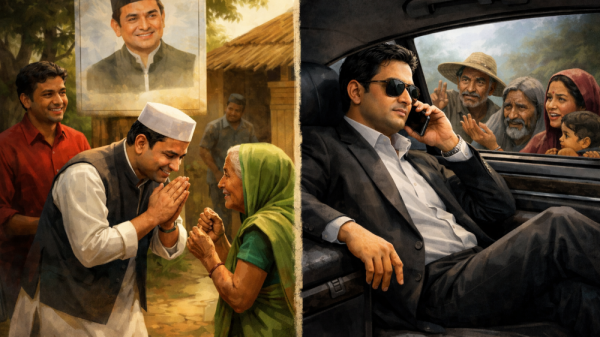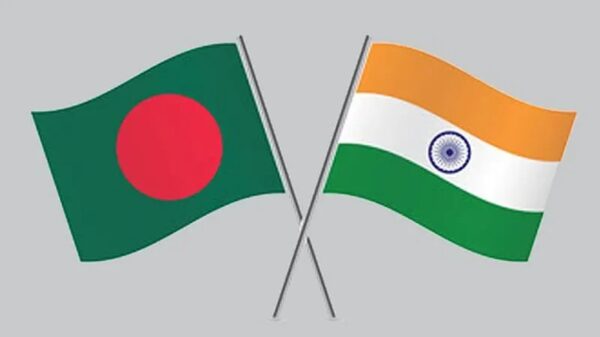AI ২০৫০ সালের ভাবনা: প্রযুক্তির জয়যাত্রা না মানবিক বিপর্যয়?
- আপডেট টাইম : শনিবার, ১৯ এপ্রিল, ২০২৫
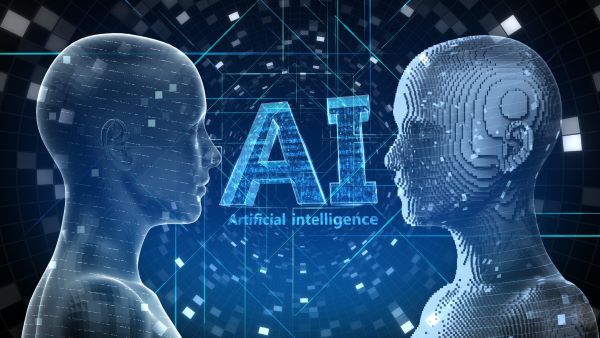
সম্পাদক : মুহাম্মদ জাকির হোসাইন
২০৫০ সাল—একটি সংখ্যা মাত্র নয়, বরং একটি দিগন্ত, যেখানে মানবজাতির প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের মুখোমুখি হওয়ার কথা। এই ভবিষ্যতের কেন্দ্রে থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)। আজ আমরা যে AI-কে কেবল তথ্য বিশ্লেষণ, চ্যাটবট বা ছবি চিনতে ব্যবহার করছি, আগামী দিনে সেই AI-ই হবে সমাজের চালিকাশক্তি। প্রশ্ন হচ্ছে—এই পথ কি আমাদের সভ্যতাকে আরও মানবিক করবে, না কি মানুষকেই মেশিনের ছায়ায় বিলীন করে দেবে?
এআই যতই বুদ্ধিমান হচ্ছে, ততই তা মানবিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা অর্জন করছে। ২০৫০ সালে একটি AI যদি আদালতের রায় দেয়, কিংবা অস্ত্রের ট্রিগার টানে, কিংবা সন্তানকে শেখায়—তাহলে সেই AI-এর নৈতিক ভিত্তি, পক্ষপাতহীনতা ও দায়িত্ববোধ কে নির্ধারণ করবে?
একদিকে AI আমাদের জীবন সহজ করে দিচ্ছে। চিকিৎসা, কৃষি, শিক্ষা এমনকি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাতেও AI ইতিমধ্যেই বিপ্লব ঘটাচ্ছে। ২০৫০ সালে ক্যানসার শনাক্তকরণ থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানে AI হবে নির্ভরতার নাম। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য AI হতে পারে ঘুরে দাঁড়ানোর হাতিয়ার—যদি তার ব্যবহার সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।
অন্যদিকে রয়েছে গভীর শঙ্কা। প্রচলিত চাকরি হারানোর আশঙ্কা, গোপনীয়তার সংকট, তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো এবং ‘সুপার ইন্টেলিজেন্স’-এর ভয়—যা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি একটি AI নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়, তাহলে তার দায়ভার কে নেবে? এই প্রশ্নই আজ নীতিনির্ধারকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে।
বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে শিক্ষা, দক্ষতা ও প্রযুক্তি ব্যবহারে এখনও বৈষম্য প্রকট, সেখানে AI-ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নেওয়া আরও জরুরি। শুধুমাত্র প্রযুক্তি আমদানি নয়, নিজেদের মতো করে ‘নৈতিক প্রযুক্তি’ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। তৈরি করতে হবে এমন এক AI-ভবিষ্যৎ, যা হবে স্বচ্ছ, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক।
২০৫০ সাল খুব দূরে নয়। আজ যে শিশু প্রথমবার মোবাইল হাতে নিচ্ছে, সেই শিশু তখন চাকরির বাজারে থাকবে। সে কি মেশিনের সঙ্গে কাজ করবে, না মেশিন তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে—সেই উত্তর নির্ভর করছে আজকের সিদ্ধান্তের ওপর।
প্রযুক্তিকে ভয় নয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করেই গড়ে তুলতে হবে এক মানবিক আগামী। AI যেন মানুষের সহায়ক হয়, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়—এই হোক আমাদের ২০৫০ সালের মূল ভাবনা।